উৎসব হলো সভ্যতার নিয়ামক। মানব জাতির ইতিহাসে এ উৎসব সময়ের হাত ধরে আজকের পর্যায়ে এসেছে। খ্রিস্ট ৩৫০০ বছর পূর্বে আর্যগোষ্ঠীর হিন্দি স্লাভভাষী মানবকুলে সর্বপ্রথম উৎসবের সূচনা ঘটে। সোমরস, সঙ্গীত, নৃত্য, বাজন ও একত্রিত হওয়াকে উৎসবের দেহ বলা হয়। প্রকৃতির দান পুষ্পের বাহারি-ব্যবস্থারও শুরু হয় তখন। তার ১৫০০ বছরের পর বক্ষুতটে (অক্সাসের তীরে) স্বাত উপত্যকায় অতীতের পুরু-জনের প্রথানুযায়ী পশু পালের সেরা ঘোড়াটি বলি দেওয়া হতো, যা ইন্দ্রপূজার বলি হিসেবে বিদিত। এতে মানুষের আমিষের চাহিদাও পূরণ হতো নতুবা গায়ে অত জোর আসবে কেন? বছরের বসন্ত শেষে অনুষ্ঠিত এ উৎসবে নারী পুরুষ, যুবক-যুবতী সকলে অংশ নিতো। এতে গোমাংস, সোমরস, মধু, ভাঙ, ফুল, নাচ উপস্থাপন করা হতো। নারীরা স্বর্ণালঙ্কারসহ বসন-ভূষণে সজ্জিত হওয়া, প্রণয় কামনা পূরণ, রজনীভোগসহ এক সামগ্রিক আনন্দ প্রকাশিত হতো এ উৎসবে। (রাহুল সাংকৃত্যায়নের `ভোলগা থেকে গঙ্গা` এর ২য় পরিচ্ছেদ-দিবা ও ৫ম পরিচ্ছেদ-পুরুধান দ্রষ্টব্য)। ভোলগারের মানবগোষ্ঠীর এ উৎসবের মালিকানা হাজার হাজার বছর ধরে ছড়িয়ে এসেছে মানুষের থেকে মানুষে যুগ-যুগান্তর। কালক্রমে গঙ্গাবাহিত মানবগোষ্ঠীর নানা শাখায় প্রবিষ্ট হয়েছে নানা স্থানে। উৎসবের বাহ্যিক রূপ নানা আঘাতে হয়তো বদল হয়েছে কিন্তু তার মূল বৈশিষ্ট্য থেকে গেছে অক্ষত।
চীনের বসন্ত উৎসব ও চান্দ্রবর্ষের ড্রাগন নৃত্য, ভিয়েতনামের চান্দ্রবর্ষের তেত উৎসব, মিয়ানমারে ছিংগ্যেয়েন এক একটি মাইলফলক। এদিকে আমাদের বাংলাদেশে সনাতনী ধারার বাঙালিদের চিরায়ত চৈত্র সংক্রান্তির সমসাময়িক পার্বত্য চট্টগ্রামেও বিভিন্ন নামে এ উৎসব পালিত হয়ে আসছে। যেমন- বিঝু, বিষু, বৈসু, সাংগ্রাই, চংক্রাণ নানা নামে পরিচিত। উৎসবের আয়োজন, আমেজ, মেজাজ মূলত: খাদ্য, আবাসন, স্মরণ, নিবেদন বা বন্দনা ও মূল্যায়ন। এ সব কৃত্যগুলো সম্পন্ন হয় সাধারণত আনন্দের মধ্যে দিয়ে, উল্লাসের মধ্যে দিয়ে। সাধারণভাবে অধুনা এটাকে আমরা নাম দিয়েছি সামাজিক উৎসব। দ্বিতীয়ত পাহাড়িদের সাধারণ চরিত্র হলো- তারা আমোদপ্রবণ ও উৎসবপ্রিয়। তাই তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় যে কোনো অনুষ্ঠান উৎসবের রূপ নেয়। জানা যায়, বিগত সময়ে রামগড় মহামুনি ও খাগড়াছড়ি য়ংড বিহারে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ মেলাগুলো ১৫ দিন থেকে ১ মাসব্যাপী চলেছে। এতেও আয়োজকদের খায়েশ পূরণ হয় না, তারা আরও প্রলম্বিত করতে চাইলে স্থানীয় ও বিহার কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হয়ে পুলিশের সহায়তা নিয়ে এগুলো বন্ধ করতে হয়েছিল।
প্রবল শীতের পর এখানে ফাগুন মাসে রাশি সংক্রমণের সাথে সাথে উত্তরীয় বায়ু প্রবাহ শুরু হয়। প্রকৃতি তখন সজীব হয়ে উঠে। গাছে গাছে ফুল-ফল আসে। কিছু প্রজাতির গাছে পাতা ঝড়ে যায়, নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে। প্রকৃতির শক্তি বলে কথা! বনে নানা রকমের পাখি লোকালয়ে পর্যন্ত চলে এসে জানান দিতে থাকে। এদের প্রজননকালও শুরু। পাখিদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে জনপদগুলো। পাহাড়েও একটা তাড়া শুরু হয়ে যায়। বাৎসরিক আয়োজনের জন্য গ্রামে গ্রামে একটা প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। কাজে-কর্মে, মননে কী এক তাগিদ দেখা দেয়। অর্জনের হিসাব নিকাশ, ক্লান্ত মনে নিজের অবয়ব ফিরে দেখার তাগাদা অনুভূত হয়। তার জন্য বাড়তি কিছু দায়িত্ব ঘাড়ে এসে চাপায়।
পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ সময় পর্যন্ত উৎসব পালন নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। এগুলো বেশির ভাগই নেরেটিভ। এখান থেকে সমাজ নতুন কোনো পথ খুঁজে পায়নি। তবে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এখনো চলমান। সম্প্রদায়গতভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্র সহজতর হবার কারণে আর গভীর চিন্তা করতে হয় না। সহজেই নতুন নতুন কর্মসূচির উপাদান পেয়ে যাচ্ছে। এক জনগোষ্ঠীর একটি উপাদান অপর গোষ্ঠীর কাছে প্রবিষ্ট যাচ্ছে দ্রুততার সঙ্গে। এতে উৎপত্তিগত নিয়ে আলোচনা ও বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এগুলো নিরসনের জন্য একটা বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণার অবকাশ ছিল। তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটগুলো এ দায়িত্ব নিতে পারতো। কিন্তু এগুলো লোকদেখানো দায়সারা গোছের কিছু গতানুগতিক ধারার উপস্থাপন করে ক্ষান্ত থাকে। এক্ষেত্রে একটা চুম্বকীয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেমন- বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে নির্ধারিত কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের কিছু নাচ-গান-আবৃত্তি কিংবা নাটক দেখিয়ে ঐতিহ্যবাহী এ সংস্কৃতি পরিবেশন করে গৎবাঁধা নিয়মে উৎসবের চাহিদা মেটায়। অথচ পরিবেশনকারীরা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কোনো প্রতিনিধিত্ব করে না। ফলে এদের উদ্দেশ্য বা বক্তব্য মূল জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছায় না। তাদের মধ্যে জাগরণ কিংবা মূল্যবোধ তৈরি হয় না।সেখানে কোনো গবেষণার কাজ হচ্ছে না তা আগেই বলেছি।সম্ভবত প্রতিষ্ঠানগুলো সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে আটকে আছে।
কারণ এ প্রতিষ্ঠানগুলোর অতীত রেকর্ড বেশ উজ্জ্বল। এগুলোর ভূমিকার কারণে একদিকে যেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লেখক ওঠে এসেছেন, অপরদিকে বিলুপ্তপ্রায় কিছু কাহিনী, তালজাতীয় কিংবা `পী` পাতায় লেখা দুষ্প্রাপ্য ডকুমেন্ট উদ্ধার করার সম্ভব হয়েছে।
এদিকে চৈত্র মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে জনগোষ্ঠীসমূহ যে উৎসব পালন করে আসছে তার একটা সামাজিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। ফলে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর একটি সম্প্রদায়ে মৈত্রী ও মমত্ববোধের সেতু রচিত হয়। তাদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা ছিল তা অনেকটা কেটে গেছে। সংস্কৃতি বিনিময় দৃশ্যমানভাবে এগিয়েছে।
ঐতিহ্যের ধারার গিলা একটা প্রাচীন উপাদান। গিলার সঙ্গে তাদের জীবনধারা সম্পৃক্ত। তাদের নিজস্ব মিথকে ভিত্তি করে পৌরাণিক কাহিনীকেন্দ্রিক ক্রীড়া চর্চার আয়োজন করে একাধিক জনগোষ্ঠী। প্রায়ই পাড়াগাঁয়ে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় এ ক্রীড়ার আয়োজন হয় গ্রামীণ আদলে।এ ক্রীড়াগুলো গ্রামীণ সমাজকে যথেষ্ট আনন্দ দেয়।
দ্বিতীয়ত অতীতের ফেলে আসা ঘটনাগুলো স্মরণ করে গানের মধ্যে দিয়ে, অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে, নৃত্যের মধ্যে দিয়ে ও আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে। এখানে চাকমাদের `বারমাসি গান` ও মারমাদের `টিছিহ্নৈলাহ্` উল্লেখ করা যায়। এগুলো নিষ্কলুষ ও চিত্তাকর্ষক। এখানে যথেষ্ট দার্শনিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। একটা থাকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, অপরটিতে থাকে জীবিকা ও অভিবাসন। এগুলোর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক রূপান্তর ঘটেছে। অবশ্য চাকমাদের গেঙখুলি, ত্রিপুরাদের গড়াইয়া নৃত্য, মারমাদের রিকাজাপোয়ে এর জন তুষ্টির বড় ইভেন্ট হিসেবে এখনো গণ্য। অপরদিকে এখানে ধর্মীয় ক্ষেত্রটাও আলোচনার দাবি রাখে। সংখ্যাগত দিক দিয়ে প্রধান কয়েকটি সম্প্রদায় অন্তত ধর্মীয় আচার প্রতিপালন করে ঘটা করে। তাদের জীবন জীবিকার প্রধান নিয়ামক হলো ধর্ম। তাই ধর্মের নীতি চর্চা করা আর এ সময়টাতে তাদের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য। তারা এ সময়ে তাদের পূজিত বৌদ্ধমূর্তিগুলোও চন্দন পানি দিয়ে ধুয়ে নেয়। তখন নানা আনুষ্ঠানিকতাও থাকে।
আবার কিছুক্ষেত্রে আনন্দ বিনিময়, বিনোদন, হর্ষ করা, পানীয় পান ও আমিষ গ্রহণ করা একটা উল্লেখযোগ্য দিক। বনের ফলমূল দিয়ে `পাঁচন` রান্না ও মুখরোচক খাবার পরিবেশন আরেকটা দিক। দেবদেবীকে পূজার জন্য বন থেকে ভিন্ন এক প্রজাতির ফুল সংগ্রহের অনুষঙ্গটিও আলোচনার দাবি রাখে। কারণ এ ফুল বছরে কেবল এ সময়টাতেই ফুটে। মনে হয় শুধু পাহাড়িদের আরাধনার কাজে ব্যবহারের জন্য এ ফুল ফুটে , অন্য সময় নয়।পাহাড়িদের এ ফুলের পৃথক পৃথক নিজস্ব নাম আছে। ধবধবে সাদা রঙের এ ফুলের স্বীকৃত বাংলা নাম আছে কিনা জানা নেই। তবে চাটগাঁর ভাষায় বিউফুল। জুতসই বাংলায় বলা যায় বনফুল।
এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়ায় বনের ওপর অত্যাচার বেড়েছে। বনের আয়তন কমেছে আশঙ্কাজনকভাবে। ফলে গত দুই দশকে পাঁচনের উপাদান ও এ লোকপ্রিয় ফুলটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেই ফুল যেমন পরিচিত নয়, তেমনি গুরুত্বপূর্ণও নয়। অথচ তাদের পূর্বসূরিরা এ সামাজিক উৎসবে এগুলো ব্যবহার করত। তার একটা সামাজিক মূল্য এখনও আছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের এ সমবেত-সামাজিক উৎসবের রূপ অনেক বদলে গেছে। এখন এ সময়ে এক বড় ধরনের বাণিজ্য চলে। বড় বড় পানীয় কোম্পানি বিভিন্ন ব্রান্ডের পণ্য নিয়ে আসে। দামী ফল, মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য এনে গুদামজাত করে রাখে এবং উৎসবকালে বিপণন শুরু করে। পাঁচন রান্নার জন্য দামী লাক্ষা, মাইট্যাসহ নানারকম লোভনীয় শুঁটকি বিক্রি হয়। সন্ধ্যায় শুঁটকি বাজারে গেলে এর আঁচ পাওয়া যায়। পাহাড়িদের পাঁচন সনাতনী সম্প্রদায়ের মতো নয়। তারা পাঁচনে শুঁটকি ব্যবহার করে না , যা পাহাড়িরা করে। অনেকে আবার পাঁচনে শুঁটকির পরিবর্তে মাংস ব্যবহার করে। তাদের উৎসবে খাবারের রুচিতেও সম্প্রদায়ভেদে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। আমিষ পূরণের জন্য বাজারগুলোতে প্রচুর মোরগ-মুরগি, শুকর, ছাগল ও অন্যান্য মাংস বিক্রি হয়। এর কারণ হলো, পাঁচন রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বন থেকে আর সংগ্রহ করা যায় না। ফলে খাবারের রুচিও বদলে গেছে। মানুষের মধ্যে নাগরিকতার ছোঁয়াও লেগেছে। নাগরিকতার একঘেয়েমি কাটাতে অনেকে পরিজনসহ গ্রামের দিকে ছুটে।
এ আয়োজনগুলো সম্পন্ন করতে এখন প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। তারপর মহিলা, শিশুদের কাপড় প্রচুর বেচাকেনা হয়। শহরকেন্দ্রিক লোকেরা দেদারসে অর্থ ব্যয় করে। প্রান্তিক এলাকার লোকজনের মধ্যে আর্থিক সঙ্গতি কম থাকায় পুরনো ধাঁচের চর্চা কিছুটা ধরে রাখতে পারছে।
পাহাড়িদের মধ্যে থেকে ব্যবসায়ী শ্রেণি গড়ে না ওঠায় তারা এ সব খাত থেকে কোনো উপার্জন করতে পারে না। আবার তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলোও তেমন আকর্ষণীয় নয় বিধায় সেদিক থেকেও তারা খুব বেশি আয় করতে পারে না। ফলে এ উৎসবে তাদের খরচের বহর খুব বেশি হয়ে থাকে। লাভের নয়, লোকসানের তালিকায় তাদের নাম।
আবার দেখা যায়, কিছু প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে র্যালি বা পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পাহাড়িদের উৎসবে এ ধরনের কর্মসূচির অস্তিত্ব কখনো ছিল না। গত শতকের ৮৬ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পাহাড়ি ও পুনর্বাসিত বাঙালিদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। সেই আঘাতে মলম দেওয়া স্বরূপ পরের বছর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা থেকে এক সম্প্রীতি র্যালি যৌথভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। পরে মারমাদের একটি সংগঠন নিজেদের লোকজন নিয়ে এ সময়ে র্যালি বের করে সম্প্রীতির নামে। এখন এ র্যালিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশ নিতে দেখা যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে প্রচুর লোকজনও অংশ নেয়। র্যালির খাতে বড় অংকের টাকা খরচ করতে হয়।
পাহাড়িদের এ উৎসব বড় ধরনের এক মিলনমেলা।একে অপরের মধ্যে এক প্রকার সম্পর্ক তৈরি করে। সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ তৈরিতে বড় অবদান রাখছে। কিন্তু বাইরের সংস্কৃতির থাবায় প্রকৃত নিয়মরীতি থেকে সরে যাচ্ছে। তা থামানো দরকার নতুবা এদের উৎসব ও সভ্যতার গতিপথ ঝুঁকির মুখে পড়বে। ঐতিহ্য হারাচ্ছে। কিন্তু পাহাড়ি নেতৃত্ব সেই দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে পারছেন বলে মনে হয় না। আর যে বিভক্তি বিরাজমান এতে কারো কোনো পরামর্শ বা উপদেশ শুনতে সমাজ প্রস্তুত নয় বলে মনে হয়। ফলে পাহাড়ের উৎসব কিছুটা কালিমালিপ্তের পথে ধাবিত হচ্ছে কিনা তা আগামীতে পরিষ্কার হবে।
একুশে সংবাদ/ব.ন.প্র/জাহা
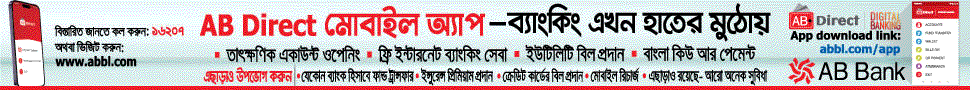







 একুশে সংবাদের সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি অনুসরণ করুন
একুশে সংবাদের সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি অনুসরণ করুন
















আপনার মতামত লিখুন :