একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনা যতো আলোচিত হয়েছে তাঁর সমাজচিন্তা ততটা আলোচিত হয় নি। যদিও এই দুই বিষয়ের আলোচনা পরস্পরের পরিপূরক। এই দ্বিবিধ মনস্কতার ভিত্তি, রূপায়ণ, যে রবীন্দ্র-সমাজে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন তাতে তাঁর গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে দ্রুত রূপান্তরিত ভারতীয় সমাজে তাঁর অভিঘাত, এইসব ব্যাপারে তাঁর মতো একজন বড়ো মাপের চিন্তাবিদের প্রতি মনোযোগ আজকে কতোটা এবং কেন সেসব কথা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়।
রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা জ্ঞান হিসেবে, ভাব হিসেবে কেমন এবং কর্মে অনুশীলনে কতোটা এ কথা ভাবা উচিত। রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে —
ক) শান্তিনিকেতন-পূর্ব জীবন (১৮৭৯ - ১৮৯১): এ পর্বে তিনি আলোচনা করেছেন— ভারতীয় হিন্দু পরিবারের ভিতরকার কাঠামো, পুরানো পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গুরুজন লঘুজন ভেদ, অধিকার ভেদ, পরিবারের মধ্যে কঠিন বিন্যাস নিয়ে। ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবী, স্ত্রী-স্বাধীনতার দাবীর কথা বলেছেন। ঐতিহ্যশক্তি ও আধুনিকতার শক্তি, স্বদেশ শক্তি ও স্বকালের শক্তির সমন্বয় চেয়েছেন তিনি। কৃষ্ণ কৃপালনী দেখান বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট, দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্বজনীন, আপন জাত, ধর্ম, নেশন প্রভাব-মুক্ত করতে চেষ্টা চালান।
এ সময়ে গুরুত্ব পাচ্ছে সমাজে ব্যক্তির অধিকার, সাম্য, ব্যক্তির স্বাধীনতা, সমাজে বা পরিবারে নারীদের বন্দীদশা। বাল্যকালীন সর্বাত্মক বশ্যতা, কঠিন পারিবারিক প্রভুত্ব-দাসত্ব, কর্তৃত্বপরায়ণ নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে, অযৌক্তিক ভক্তির দাবীর বিরুদ্ধে তর্ক তুলেছেন। ব্যক্তির মূল্য, ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রার্থিত ছিল, তবে প্রাচ্যাভিমান ছিল। বাল্যবিবাহের অযৌক্তিকতা নিয়ে স্পষ্টবাক্। শিলাইদহ পর্ব এ সময়েই। এ কালে কর্মী রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস আলোচ্য হবে, পরে।
খ) শান্তিনিকেতন - বঙ্গদর্শন পর্ব (১৯০১ - ১৯০৭): ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন, নৈবেদ্য রচনা প্রভৃতিতে ছিল হিন্দুত্বের ঘোর। বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথার বিরুদ্ধে থাকলেও মেয়েদের বিয়েতে নিজমতের বিরুদ্ধে যেতে হয়। বিধবা বিবাহ-ও রথীঠাকুরের বিয়েতে ঘটল। শাশ্বত ভারত, মুমূর্ষু ভারতের উজ্জীবন ব্রাহ্মণের দ্বারা - এসব বিশ্বাস ছিল। ১৯০৪-তে ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাজ ও স্বদেশচিন্তা বিষয়ে সুস্পষ্টতা এল। চাইছেন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টানের মৈত্রী। তবে দেশচেতনার সঙ্গে ধর্মচেতনা, ভারতচেতনার সঙ্গে হিন্দুত্বচেতনা মিশে ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় স্বদেশী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশীতে দীক্ষাগ্রহণের, জাতির আত্মআবিষ্কারের, জাতীয় ঐক্যের আন্দোলন। অন্যান্য নেতারা যখন মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষাকেই প্রধান মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ সেকালে বোঝেন পল্লী-উন্নয়ন, পল্লীবাসীর আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনা, পল্লীবাসীকে সংগঠিত করা। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও রবীন্দ্রনাথ কি যাবতীয় পল্লীবাসীর উন্নয়ন, আত্মপ্রত্যয় ফেরানোর, পল্লীবাসী সবাইকে সংগঠিত করতে পেরেছিলেন? শিলাইদহ পর্বে স্বল্পপ্রয়াসী হলেও এ শুভৈষা কি আজীবন ফলবতী হয়েছিল?
গ) চূড়ান্ত পর্ব: ইংরেজ যে এদেশের অধিবাসী হতে আসেনি, এসেছে শোষণ করতে, এটা তাদের উপনিবেশ মাত্র - এ অপ্রিয় সত্য বহুকাল তাঁর নজরে আসেনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — ‘যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া চলিয়াছে, ইংরেজ সেই ভারতবর্ষের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ — আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কি অধিকার আছে?’ (শিক্ষার মিলন) এ চিন্তা ভ্রান্ত। কোনটা অসময়, কোনটা সুসময় এটা কিভাবে ঠিক হবে? ছোট ইংরেজ, বড় ইংরেজ চিন্তাও এ প্রসঙ্গেই স্মতর্ব্য। ‘নারীর মনুষ্যত্ব’ পত্র প্রবন্ধে (১৯২৮) তিনি নারীর আত্মমর্যাদা, নারীর আত্মতা, নারীর মনুষ্যত্বের কথা বলেছেন। এ চিন্তার সামাজিক ও শিল্পিত অভিব্যক্তি দিতে সমর্থ হয়েছেন তিনি। একটি চিঠিতে (১৯৩৪) ইংরেজ শাসন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মোহমুক্ত মনের পরিচয় অবশ্য পাওয়া যায়। অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি বলছেন ইংরেজ এদেশে যা যা করেছে তা ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি হিসেবেই করেছে। সাম্রাজ্য অটুট থাকবে; ধনতন্ত্র অটুট থাকবে, অথচ ভারতবর্ষে ইংরেজ অন্যরকম আচরণ করবে এটা কখনই সম্ভব নয়। রবীন্দ্র উপলব্ধি হল — মানবসভ্যতার যে রূপ সামনে তা মানুষখাদক, এবং সভ্যতার ভিত্তিবদল না হলে আমরা বাঁচব না। অমিয় চক্রবর্তীকে বলা একথা তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ বা ক্রোধের জন্ম দেয় নি। ঔপনিবেশিক শাসন যদি মানুষখাদক হয় তাহলে তাকে দূর করার জন্য স্বদেশীদের জেহাদ বা নিপীড়ন মেনে নেওয়া সমালোচ্য কেন? ‘কালান্তর’ গ্রন্থের ‘নবযুগ’ প্রবন্ধে আশা প্রকাশ করেছিলেন — সম্ভবত আমাদের দুর্গতির রাত্রি-অবসান খুব দূরে নয়। ১৯৩৩ এর এই প্রবন্ধের পরে ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ। তাঁর এ বাণী যদি সত্য হত তাহলে বহু নিগ্রহের পর স্বস্তি নামত। কিন্তু চল্লিশে, পঞ্চাশে, ষাটে আমরা দুর্গতির রাত্রি অবসানকে প্রত্যক্ষ করতে পারিনি। একে দুর্ভাগ্যই বলা যেতে পারে।
রবীন্দ্রনাথের পল্লিসংগঠনের কিছুটা পরিচয় নেওয়া যাক। এর দুটি পর্যায় — শিলাইদহ পর্ব এবং শ্রীনিকেতন পর্ব। ঠাকুর এস্টেটের পার্টিশনের পর থেকে (১৮৯৫) অন্ততঃ কুড়ি বছর রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জমিদারির অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে চাষির অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব পেলেন, শিলাইদহ, বিরাহিমপুর, সাজাদপুর তদারক করতে হত (১৩০১/১৮৯৪)। স্বদেশী সমাজ (১৯০৪), কিছু পরের তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ।
১৯০৭ সালে পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন গ্রামে উন্মাদের মতো মোকদ্দমা চলছে, ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ ফিরে ফিরে আসছে কিন্তু আকালে খিদে মেটানোর সঞ্চয় নেই। রবীন্দ্র পরামর্শ ছিল — ‘শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার-সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্থাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত করো।’
এই উদ্দেশে তাঁর জমিদারিতে কয়েকটি পল্লী একত্র করে মণ্ডলী, মণ্ডলীতে এক একজন প্রধান নিযুক্ত করা হল। ইনি নির্বাচিত প্রধান। বিচারের জন্য হল সালিশী সভা।
দেশের উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়, রপ্তানির উদ্যোগ নেওয়া হয়। বেত, বাঁশ, খড়, খেজুরপাতা, আনারসপাতা, পুরোনো কাপড়, পাট প্রভৃতি দিয়ে শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রির ব্যবস্থা। চিঠিতে (১৯০৮) লেখেন — ‘বছরে বেশ কয়েকমাস চাষীদের কোন কাজ থাকে না। এই সময়ে হাতের কাজ করে তারা অনায়াসে কিছু রোজগার করতে পারে।’ কালীমোহন ঘোষকে পতিসর নিয়ে এলেন ধানভানা কলের ব্যবস্থা করার জন্য। জামাই নগেন্দ্রনাথকে লিখছেন — ‘দেশের গো-সম্পদের উন্নতি করতে হবে। অন্যথায় চাষবাস বন্ধ হয়ে যাবে। দুধ, ঘি, দুর্মূল্য ও ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হবে।’ কো-অপারেটিভ করার তাগিদ অনুভব করছেন। কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যা সম্পর্কে উন্নত শিক্ষাগ্রহণের জন্য রথীন্দ্রনাথকে, নগেন্দ্রকে, সন্তোষকুমার মজুমদারকে আমেরিকায় পাঠান। পল্লী সংগঠনের প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ হিতৈষিবৃত্তি ও কল্যাণবৃত্তি চালু করেন। বৃত্তির টাকা ব্যয় হত প্রজা উন্নতিতে। শিলাইদহ-কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৫০ বিঘা জমিতে আলুচাষ করা হয়। সহায়ক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি মাটি পরীক্ষার পর জমি তৈরি করে নৈনিতাল আলু চাষ হয়। বীজ আলু সংগ্রহের ভার নিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। রথীন্দ্র আমেরিকা থেকে ভালো ভুট্টার বীজ আনান। চাষীদের আলু ও টমেটোর চাষ শেখানো হয়। ইলিশমাছ কিনে তাতে চুন মাখিয়ে মাটির নীচে পুঁতে সার বানান রথীন্দ্র, যে সার চাষীরা কাজে লাগায়।
টাকা প্রতি তিন পয়সা আদায়, সম পরিমাণ অর্থ আদায় এস্টেট থেকে। প্রজা উন্নতি তথা রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত, উপাসনালয় সংস্কার ও সংরক্ষণ, স্কুল মাদ্রাসা স্থাপন ও চালানো, চাষীদের বিপদে-আপদে সাহায্য, কূপ খনন, দিঘি ও পুকুর পরিষ্কারও ছিল। জমিদারি ও গ্রামবাসীর টাকায় যৌথ উদ্যোগে অনেকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় পতিসর ও শিলাইদহে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। শিলাইদহে স্থাপিত হয় মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়। পতিসরে হাসপাতাল এবং কালীগ্রাম পরগণায় চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল। ১৯০৭ সালে অজিত চক্রবর্তীকে চিঠিতে বলেন — ‘আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজ স্থাপন করতে চাই।’ কিন্তু ইংরেজ প্রশাসনকে উপেক্ষা করে তা কিভাবে সম্ভব? চাষীরা প্রথমে সন্দিহান হলেও ফসলের উৎপাদনে ক্রমশ আকৃষ্ট হয় এবং উৎসাহিত হয়ে কাজে নেমে পড়ে। পদ্মা থেকে প্রচুর ইলিশ কলকাতায় রপ্তানি হত, মাছ নেওয়ার ব্যবস্থা বা সংরক্ষণের উপায় ছিল না। রথীন্দ্র কয়েক নৌকা-বোঝাই মাছ অল্পদামে কিনে চুন দিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করলেন। এক বছর পর তৈরি হল চমৎকার সার। আনারসের পাতা থেকে আঁশ বা সুতো-ও তৈরি করা হল। কবি পতিসরে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করলেন - ফলে মহাজনি কারবার বন্ধ হয়ে যায়। শত্রু বাড়তে থাকে। কৃষিব্যাঙ্ক ভালোই চলছিল। নোবেল প্রাইজের লক্ষাধিক টাকা ওই ব্যাঙ্কে রাখা হল। ঐ টাকার সুদ দিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ, শান্তিনিকেতনের কিছু খরচও চলত। Rural Indebtedness আইন প্রবর্তিত হবার পর প্রজাদের যে টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল তা আদায় করে গেল না। নোবেল প্রাইজের আসল টাকা ব্যাঙ্ক বিশ্বভারতীকে ফেরৎ দিতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ জাহাজের খোল কিনে ইঞ্জিন বসিয়ে দেশী বাষ্পীয় পোত, দেশলাই তৈরি, কাপড়ের ও পাটের কল চালানো, আখমাড়াইয়ের কল কেনাবেচা প্রভৃতি ব্যবসা বাণিজ্যের চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হন নি। দেওঘরের কাছাকাছি ন’টি মৌজা পত্তনি নিয়ে কয়েকজন দেশানুরাগী এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গে মিলে The Deoghar Agricultural Settlement Company নামে একটি প্রকল্প স্থাপন করেন, রিখিয়া এবং অনুরূপ কটি স্বাস্থ্যকর জায়গায় স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের সংকল্প ছিল। কিন্তু এ প্রকল্পও স্থায়ী হয়নি। রথীন্দ্র লিখেছেন যতদিন কৃষিব্যাঙ্ক ছিল বহু বছর ধরে বিদ্যালয়ের ওপরে বিশ্বভারতীর বছরে আট হাজার টাকা করে একটি স্থায়ী আয় ছিল। এই ব্যাঙ্কের শেষ চিহ্ন ছিল শান্তিনিকেতন কল্যাণকোষে। কারো কারো মতে মহম্মদ ইউনুস যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বিস্তার করেছেন রবীন্দ্রপ্রয়াস তার পূর্বসূরী। সন্দেহ নেই রবীন্দ্রনাথের এই সব প্রয়াসের পিছনে কাজ করেছে দেশপ্রেম, আত্মনির্ভরতা, রাষ্ট্রনির্ভরতায় ঔদাসীন্য।
রবীন্দ্র প্রবর্তিত গ্রামীণ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় শ্রীনিকেতনে। কৃষিবিদ লিওনার্ড এলমহার্স্টের সক্রিয়তায় এবং অর্থানুকূল্যে ব্যাপকভাবে গরীব গ্রামবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য শ্রীনিকেতনের কর্মধারা শুরু হয়। বোলপুরের অনতিদূরে সুরুল গ্রামের কুঠিবাড়িটি সিংহ পরিবারের থেকে কিনে কৃষি গবেষণার্থে শ্রীনিকেতন শুরু হয় ১৯১৪-তে। কৃষির উন্নতি হবে। হস্তকারুশিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগও নেওয়া হয়। ১৯২২ থেকে শিল্পভবন কার্যকরী ভূমিকা নেয়। হস্তকারুশিল্প - যেমন চামড়া, সূঁচ, মাটি ও গালার কাজ, শতরঞ্চি বুনন, ব্লক ছাপা যন্ত্র চলতে থাকে। বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্প সংগ্রহে উদ্যোগ নেওয়া হয়। চট্টগ্রামের মহিলাদের শিল্প, লক্ষ্মীপূজা বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে আলপনা, শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালির শিল্পদ্রব্য, মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ, শাড়ির পাড়ের নকসা ইত্যাদি ব্যবহৃত। এর সঙ্গে আশা করা হত গ্রামীণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছে শেখা হবে লোকসঙ্গীত, লোকসাহিত্য, টোটকা, ছড়া, বচন। কালীমোহন ঘোষ আদিবাসী কল্যাণ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সালিশী বিচারে বিবাদ মেটানোতে অগ্রণী ছিলেন। তিনি কেঁদুলি, কঙ্কালিতলা ও অন্য মেলায় ব্রতী বালকদল নিয়ে গিয়ে মদ, তাড়ি, জুয়া ও দুর্নীতি নিবারণে, মেলাক্ষেত্রের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সাহায্য করেছিলেন। আর ছিলেন আমেরিকান সমাজসেবিকা গ্রেচেন গ্রীন। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কাজে নিপুণ। ১৯২৬ সালে তাঁরই চেষ্টায় শ্রীনিকেতনে ডাক্তারখানা স্থাপিত হয়। ১৯২৭-তে প্রতিষ্ঠা হল সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। অবশ্য তার আগেই ছিল স্থানীয় উদ্যোগে তৈরি পল্লীউন্নয়ন সমিতি, সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি, ধর্মগোলা, কৃষিঋণদান সমিতি, সেচ সমবায় এবং সমবায় বয়ন সমিতি।
মেলার গুরুত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। শিলাইদহে ১৯০৫-এ আয়োজন হয়েছিল কাত্যায়নী মেলার। এর দুবছর পর ঐ অঞ্চলে হয় রাজরাজেশ্বরী মেলা। শ্রীনিকেতন পর্বে পৌষমেলা, শ্রীনিকেতন মেলা হয়; লক্ষ্য ছিল — গ্রাম ও শহরের সংযোগ-সাধন, গ্রামীণ কুটিরশিল্পের বিক্রয় এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীয় পরিচয়-সাধন। বর্তমান সময়ে পৌষমেলায় বিশেষ করে শহর প্রাধান্য পেয়েছে, ভাড়া ও অন্যান্য খরচ সামলাতে না পেরে, পাইকারদের পাল্লায় পড়ে যথার্থ গ্রামীণ শিল্পীরা যোগদানে কুন্ঠিত হয়।
জনৈক লেখক শ্রীনিকেতন-কেন্দ্রিক কাজের তালিকা পেশ করেছেন। তা হল ছাত্রদের নিয়ে উন্নত ধরনের কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা, গ্রাম্য যুবকদের ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ, গবেষণাগারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উপকরণের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, সমীক্ষা মাধ্যমে কৃষিব্যবস্থার সমস্যা উদঘাটন ও সমাধান প্রয়াস, প্রয়োজনীয় ও পরিচিত ফসল ছাড়া বিভিন্ন ফসলের চাষ, উন্নত ধরনের বীজ, ফলের চারা, উন্নতমানের পশু চাষীদের মধ্যে বিতরণ ও উৎপাদনে উৎসাহ, আবহাওয়া ও মাটির সঙ্গে মানিয়ে নানা ফসল চাষ, প্রয়োজনীয় জলসেচ ও সুচারু পয়:প্রণালী বিন্যাস, ট্রাক্টর ও রাসায়ানিক সারের ব্যবহার, উন্নত মানের জৈবসার তৈরি, অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে গোখাদ্য চাষ, উন্নত মানের গরু, ছাগল, মৌমাছি, মাছের চাষ, উৎপন্ন পণ্যের বাজার দর যাচাই ইত্যাদি। শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্রে রেখে সমবায় আন্দোলন ছড়ানো। বল্লভপুরগ্রামে পাশের গ্রামের সাহায্য নিয়ে ১৯২৬-এ কাজ। শ্রীনিকেতনের এক গ্রামসেবক বল্লভপুর প্রেরিত হন।
তবে বিরাট কর্মযজ্ঞ আশানুরূপ সাফল্য পায় নি। কারণ কৃষকদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, সংগঠন বা সংঘশক্তির অভাব এবং রাষ্ট্রের নীরব ভূমিকা। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি পাবার পর শ্রীনিকেতন-কেন্দ্রিক কৃষিবিকাশ গুরুত্ব হারায়। স্বীকার্য, প্রসঙ্গ ও প্রস্তাবগুলি সর্বকালীন, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিকূল সমাজে প্রসারিত হয় নি।
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পল্লী পুনর্গঠন পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার-পরিষেবা কর্মসূচিতে আনতে। শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠন বিভাগ পরিচালিত গ্রন্থাগার প্রথাগত শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্য উপযোগী গ্রন্থ ব্যবহার করতে দিত, স্থানীয় গ্রামীণ মানুষের জন্যও বইপত্র ছিল। ১৯২৫-এ চালু হয়েছিল চলন্তিকা বা Circulating Library. এককালে গ্রামকর্মীরা পায়ে হেঁটে যেতেন বই নিয়ে গ্রামে গ্রামে। পরে এই কাজে সাইকেল ব্যবহার হতে থাকে। ১৯২৭ সালে স্থাপিত হয় পল্লী-সংগঠন বিভাগ লাইব্রেরী, যাতে কৃষি ও গোপালন, হস্ত ও কুটির শিল্প, বিদ্যালয়-পাঠ্য এবং রেফারেন্স বইপত্র থাকে।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর বছর দুই আগে (ভাদ্র ১৩৪৬) শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় বলেছিলেন — ‘আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোট গ্রাম। আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরি হবে — এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনো সেই কথা মনে হচ্ছে।’
পল্লীআদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লালিত আদর্শের সঙ্গে এই অভিলাষ মিলে যায়। আজ প্রয়াণের ছিয়াত্তর বছর পরে কোনো উৎসুক ব্যক্তি যদি গ্রাম পরিক্রমা করেন তাহলে তিনি এই ‘জয়’ বা ‘মুক্তি’ কতোদূর প্রত্যক্ষ করতে পারবেন? এজন্য রবীন্দ্র-আদর্শকে, শুভ ইচ্ছাকে দোষ দিতে চাই না। সত্যি সত্যিই একটা কালে এই জয় বা মুক্তি সম্ভব হয়েছিল - তার বিবরণ আছে। কিন্তু আজ? সমাজসেবার জন্য উৎসাহ লাগে, টাকা লাগে। রবীন্দ্রনাথের প্রকল্পে শিলাইদহে, শ্রীনিকেতনে উৎসাহী লোকজন ছিল যারা রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে অভিভূত ছিল। এই ধরনের প্রকল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যা টাকা পয়সা উপকরণ লাগে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজ নেই। ফলে প্রয়াস ক্ষণজীবী হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত: রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের লোলুপতা ক্রমপ্রসারমান। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রয়াসের সঙ্গে এর দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। আর যাদের জন্য এই সব কল্যাণপ্রকল্প তাদের চারিত্রিক ও বিবেকগত সততাও বিরল। ফলে ২/৪-টে উদাহরণ থাকলেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বয়কট করা সম্ভব নয়, হাত মিলিয়ে চলাটা কোথাও কোথাও ‘কিছুটা’ সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — ‘যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্নতন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল।’ কিংবা — ‘আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট পরিচয়। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা। ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অস্পষ্ট পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।’ একথায় অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু শান্তিনিকেতনে এসে ঘাঁটি করার পর শিলাইদহ পরিবেশ গেছে, বীরভূম জীবনকেও দেখেছেন কিন্তু কর্মীসত্তা নানা কারণে গৌণ থেকে গৌণতর হয়ে গেছে। গ্রামগুলোকে স্বনির্ভর, আধুনিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করা কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কতিপয় সেবাব্রতীর দ্বারা সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০-এ বলছেন ‘আশা ছিল আমাদের জমিদারি যেন প্রজাদেরই জমিদারি হয়।’ কিন্তু ‘দেনার অঙ্ক বেড়ে যাওয়ায়’ তা সম্ভব হয় নি। স্বাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক হলে এ আশা ফলবতী হওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যে, তাঁর গল্পে উপন্যাসে এই সমাজকল্যাণ প্রকল্পের ছবি নেই। সাহিত্যে সমাজচিন্তা আসতেই পারে, রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে নাগরিক সমাজ কিছুটা থাকলেও গ্রাম সমাজ উপেক্ষিত। বিশেষত: মধ্যযৌবনের পর থেকে, ‘গোরা’-র পর থেকে নানা গ্রামীণ সমস্যা ও সংকট উপেক্ষিত।
আরো কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট করা যাক। ১৮৮৫ সালের বীরভূম-বাঁকুড়া-বর্ধমান জেলার দুর্ভিক্ষে রবীন্দ্রনাথ অর্থ সংগ্রহের জন্য গান রচনা করেন, প্রবন্ধ লেখেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ত্রাণভাণ্ডারে ঠাকুরবাড়ির পক্ষ থেকে ৫০০ টাকা দান করেন। সংগৃহীত অর্থে ৫২৬৩২ জনকে অন্ন দেওয়া হয়। অমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে (১৫ নভেম্বর, ১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথ বলেন — ‘শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লী সঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।’ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন — আমাদের দেশে পল্লীসঞ্জীবনের কাজে প্রথম পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয়, অর্থাৎ পল্লীসঞ্জীবনে প্রধান সহায়ক - পাশ্চাত্যবাসী এলমহার্স্ট এবং প্রাচ্যবাসী কালীমোহন ঘোষ। ১৯২০-তে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণকালে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থী এলমহার্স্টের সঙ্গে তাঁর আলাপ। রবীন্দ্রনাথ বলেন আমার বিদ্যালয় লোকালয়ের অংশ। আমি বিদ্যালয়ের জীবনকে সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই।
আমার নিজের দশ বছর শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা এবং চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে চাই রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াস ক্ষণকালের জন্য হলেও দীর্ঘকালের জন্য বাস্তবায়িত হয় নি। শান্তিনিকেতনের ‘বি. টিম’ ছিল শ্রীনিকেতন। গ্রামজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এককালে কালীমোহন প্রভৃতির লোকঘনিষ্ঠতায়। পরে তা শিথিল হয়ে আনুষ্ঠানিক হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এলমহার্স্টকে বলেছিলেন শ্রীনিকেতনে আধুনিক রীতিপদ্ধতিতে চাষ করাতে চান। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষ মজুমদার, কালীমোহন ঘোষ, গৌরগোপাল ঘোষ, সন্তোষ মিত্রকে এলমহার্স্টের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। সুরুলের কুঠিবাড়ি কিনে নিয়ে গ্রামোদ্যোগ পর্বের সূচনা করেন। উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় পতিসরে ও শ্রীনিকেতনে - কিন্তু তা ক্ষীণায়ু। শ্রীনিকেতনে কাঠ কাটা, জল তোলা, রান্নাবান্না, ঝাড়পোঁচ, পায়খানা সাফ, হিন্দু মুসলমান চাষীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা এই টিমের দ্বারা শুরু হয়। এলমহার্স্ট তো বলতেন — আই অ্যাম চাষা। পোলট্রির কাজ শুরু হয়, গ্রেচেন গ্রীনের উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়, কালীমোহনের তৎপরতায় সমগ্র গ্রামই ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতায় আসে, নামমাত্র ব্যয়ে চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এলমহার্স্ট চলে যাওয়ায়, তার টিম অক্ষম হয়ে পড়ায় এই সাধু সংকল্প ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। অস্বীকার করছি না রবীন্দ্রনাথ ও এলমহার্স্ট প্রবর্তিত শ্রীনিকেতন পরিকল্পনা পরে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের কাঠামো হিসেবে অনেকটা ব্যবহার করা হয়েছে। এলমহার্স্ট জানান ১৯২১-এ দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন শান্তিনিকেতনে রাজনৈতিক প্রভাব জোরদার। ১৯৩০-এ বার্লিন থেকে নির্মলকুমারী মহলানবীশকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন কালীমোহন অসুস্থ, তার ওপর পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে। শ্রীনিকেতনের সূচনা ১৯২১-এ। রবীন্দ্রনাথ চিন্তান্বিত, তড়িঘড়ি সুরুল-কেন্দ্রিক গ্রামোন্নয়ন যজ্ঞে যুবকদের একাংশকে লাগালেন। পুলিসী নজর থেকে মুক্ত রাখার জন্য কালীমোহন প্রভৃতিকে পতিসর প্রভৃতি থেকেও সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যাহোক কালীমোহনই অন্যতম ব্যক্তি, তিনিই গ্রামবাসীদের ‘contact man’, এদিকে শান্তিনিকেতনে যারা রাজনীতিতে আগ্রহী তাঁরা ‘looked with scepticism, and even with distaste, at the poet’s new venture at Surul.’ (‘Poet and Plowman’, Pg. 9) টাকাপয়সার টানাটানি হবে বলে শান্তিনিকেতনের অনেকেও গ্রাম পুনর্গঠনে অনাগ্রহী। ছাত্র সমস্যাও ছিল। শান্তিনিকেতনের বি. টিম শ্রীনিকেতন - আগেই বলেছি। এলমহার্স্ট-এর কথা থেকেও তার ইঙ্গিত মেলে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর নাতি সুবীরকে সুরুলে ট্রেনিং দিতে আপত্তি জানান। ওখানে দিনের অনেকক্ষণ হাতে কাজ, ঘরে মাছির উপদ্রব এসবও কারণ। যদিও সুবীরের আগ্রহ ছিল। সত্যেন ও সুবীর শ্রীনিকেতন ত্যাগ করতে চাইলে তাদের কলকাতা পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। সত্যেন স্বরাজ-কর্মে সংকল্পিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ এন্ড্রুজকে ডেকে পাঠিয়ে রাজনীতির পাঠ্যক্রমের জন্য তাঁকে তিরস্কার করেন এবং বিদ্যায়তনকে রাজনীতিমুক্ত করতে সাহায্য চান।
এলমহার্স্ট সূত্রে জানা যায় সুরুলকর্মে টাকা দিচ্ছিলেন আমেরিকার মিসেস ডরোথি স্ট্রেট। অনেক টাকা দেন। Poet and Plowman বইয়ের শেষে ১৯২৬ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত এলমহার্স্ট-ফান্ড থেকে বিস্তর টাকা দেওয়ার তালিকা আছে। তৎকালীন সরকারী সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। বলার কথাটা হচ্ছে, রবীন্দ্রকথিত স্বনির্ভরতার কর্মকাণ্ডে বাইরের টাকাপয়সা বিস্তর ছিল। এলমহার্স্ট ইলামবাজার অঞ্চলে সেরিকালচার বা রেশমগুটির চাষে তৎপরতা দেখান। এক ব্রাহ্মণ জমিদার আলুর রোগ দমনের কথা বললে, এলমহার্স্ট নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব দিলে জমিদারের আপত্তি। প্রজারা বেশী জেনে যাবে, তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। পাঠশালায় আপত্তি নেই, নিজেদের ছেলেরা উপকৃত হবে। ১৯২২, ২৮ ফেব্রুয়ারী ডায়েরিতে এলমহার্স্ট লেখেন — ক) বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ থেকে সন্তোষ বোস শ্রীনিকেতন কাজে হাত লাগাবে; খ) সুরুলের তাঁতিরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে শ্রীনিকেতনে কাজ করবে; গ) মুসলমান চাষীরা আগ্রহী হয়ে সমবায় গড়বে, শিক্ষক নিযুক্ত করবে, ডাকঘর করবে; ঘ) সুরুলের জমিদার কার্তিক সরকার গ্রামের স্কুলে আগ্রহী, শিক্ষকের বেতন দেবে; ঙ) যতীনবাবু এখানে বাড়ি করবে, হিসেব দেখবে; চ) গ্রামের ছেলেরা নিজ নিজ বাড়িতে বাগান করবে, গড়া হবে একটা গার্ডেন ক্লাব। এন্ড্রুজ একান্তে এলমহার্স্টকে বলেন যে শান্তিনিকেতন আশ্রমের একটি গোষ্ঠী সুরুলের কাজকর্মে সন্দিহান - সংঘাত সম্ভাবনা এড়াতে হবে। ডেয়ারীর কর্মীরা ছুটির দিনে তাদের দাবীমতো ওভারটাইম না দেওয়ায় শিল্পোৎসব বয়কট করে, গরুর দুধ দোওয়া, গরুকে খাওয়ানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা কিছুই করছিল না। গোরুগুলো যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল, মৃত্যুর আশঙ্কাও ছিল। অর্থাৎ সেবাধর্ম লোপাট। ‘এর ফলে শ্রীনিকেতনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বসেছে।’ (‘ভগ্ননীড় বিশ্বভারতী’, পৃ. ৫৩) গৌরগোপাল ঘোষ পড়ার সময় এবং পরে যোগ্য অধিনায়ক। এলমহার্স্টের তিন সেনানায়ক — সন্তোষ, কালীমোহন, গৌর। শ্রীনিকেতন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হলে ইনি অধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের সেতুবন্ধন রচয়িতা। শান্তিনিকেতনেও অধ্যক্ষ, কর্মসচিবের সহকারী হয়েছেন। তাঁর বিয়ের উৎসব উল্লেখযোগ্য। নন্দলাল ও সুরেন করের পরিকল্পনায় গোরুর গাড়িতে করে বর আসে। বরকর্তা রথী, তত্ত্বপ্রেরক প্রতিমা। তত্ত্ব নিয়ে এল সাঁওতাল মেয়ের মস্ত দল - বাসন্তী রঙে ছোপানো শাড়ি, রুপোর গয়না, খোঁপায় লাল জবা। রথের পাশে পাশে সাঁওতাল যুবকের দল বাসন্তী রঙের ধুতি পাগড়িতে, কাঁসর মাদল বাঁশি বাজিয়ে, পাশে সুসজ্জিতা সাঁওতালি মেয়েরা চলে নেচে নেচে। বোঝা যায় সাঁওতালদের সান্নিধ্য এবং ব্যক্তিগত কাজ হয়ে উঠত সমগ্র আশ্রমের কাজ। সৌন্দর্যময় ও আনন্দময় করার এই প্রয়াস ‘তখনো অব্যাহত’ বলে হীরেন্দ্র দত্ত দুঃখ করেছেন।
আমাদের দেশ ভক্তিবাদের দেশ। দর্শন নঞর্থকত্ব বাদ দিয়ে শুধু সদর্থক প্রসঙ্গের আলোচনাই বিধেয় — এটাই শেখানো হয়। বিশ্বভারতীর এক সময়ের উপাচার্য নিমাইসাধন বসুর মতে — বিশ্বভারতীর তিনটি মূলরূপ — ক) পরীক্ষা মারফৎ ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা, খ) জাতীয় সংস্কৃতির চর্চা, বিকাশ, প্রসারের প্রধান কেন্দ্র, অনুপ্রেরণা ও নব সৃষ্টির উৎস গ) আর্ন্তজাতিক ভূমিকা। (‘ভগ্ননীড় বিশ্বভারতী’, পৃ ৯৬-৯৭) আমার দশ বছরের শিক্ষক হিসেবে, চল্লিশ বছরের পর্যটক হিসেবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখেছি, শান্তিনিকেতনে একবার আনন্দ পাঠশালায় প্রবেশ করলে পি.এইচ.ডি পর্যন্ত তরী চলবেই। কথাটি যদি সত্য হয় তাহলে ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট দান নির্বিচার। বহু বেনোজল পবিত্র জল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শিক্ষকতা ক্ষেত্রে দুর্নীতি নানা প্রকারের - তার বিশদ বিবরণ দিতে চাই না, কিছু কিছু লেখালিখি হয়েছে। জাতীয় সংস্কৃতির চর্চা অনেকটাই আনুষ্ঠানিক, প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থা আছে কিন্তু অন্যভাষীদের আদৌ উৎসাহ নেই, উৎসাহ দেবারও কেউ নেই। আন্তর্জাতিক ভূমিকাও অনেকটা আনুষ্ঠানিক। দু-চারটে বই বা প্রদর্শনী হয়েছে, হচ্ছে; ফরাসী, জার্মান, চীনা, জাপানী ভাষা শেখানোর আয়োজন আছে। কিন্তু উৎসাহ নেই। ডেলিগেটরা বাইরে যাচ্ছে কিন্তু বেড়ানো ছাড়া কিছু হচ্ছে না। রবীন্দ্রপ্রচারের বক্তা হিসেবে বর্হিদেশে যাওয়া সুযোগসন্ধানী এমন অনেককে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি যারা রবীন্দ্রনাথ পড়া, অর্জন করার বদলে টাকা আনা পাই কনট্যাক্ট-করণে পারদর্শী। নিমাইবাবু যে ‘মানব ঐক্য’র কথা বলেছেন তা সত্য হয় নি, যা হয়েছে তা হল — স্বার্থের ঐক্য। তার একটি উদাহরণ — অকৃতকার্য সন্তান-সন্ততিকে পাশ করিয়ে দেবার দাবীতে পথ অবরোধ। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একাধিক বার এক্সকারশানে গিয়ে দেখেছি তারা দিনগুলিতে একবারও রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করে না, রবীন্দ্রনাথের গান ভুলেও গায় না। ‘ভগ্ননীড় বিশ্বভারতী’ নামক ছোট্ট বইটিতে শ্রীযুক্ত বসু বিনয় ও আশা বজায় রেখেও যেসব মন্তব্য করেছেন সেসব কথা তুলি — ১) একটি হোস্টেলের তিনটি ছাত্রী ভবনের অধ্যক্ষের সই নকল করে বাড়ি যাবার অনুমতিপত্র জমা দিয়ে বাড়ি চলে যায়। (সই নকল করে বাড়ি নয় বোলপুরে রাত কাটানোর গল্পও আমি শুনেছি)। বিদ্যাভবন ছাত্র হোস্টেলে উপলক্ষ্য খুঁজে নিয়ে উৎসবে মদের বন্যা বয়। অন্ধ সেজে শিক্ষক, পুঁথি-রিডার ডিপার্টমেন্টাল রিডার হিসেবে নিযুক্ত হয় এবং অরিজিন্যাল সার্টিফিকেট সমূহ দেখায় না এসব চাকরি করার সময়ই দেখেছি। ২) বিশ্বভারতীতে ভাল ছাত্র আসার কথা বলেছেন। কিন্তু দুটি অন্তরায় — ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা অতি সীমিত যা নীচু থেকেই ভর্তি থাকা এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আসা প্রার্থীদের অনেক অনেক পরে অ্যাডমিশন টেস্ট করা। ৩) শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষকের সংখ্যা দূরবীক্ষণ দিয়ে খুঁজতে হবে। সকলেই চাকরী-সর্বস্ব, ভোগ্যপণ্য মনস্ক। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র গ্রন্থাদির সজ্জা বেদনার, বই ইস্যু হয় অতি স্বল্প। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বুক র্যাকের ফাঁকে কর্মীদের একাধিক ভোজনসভা স্বচক্ষে দেখেছি। প্রভাতী চায়ের দোকানে কর্মী বা শিক্ষকরা রবীন্দ্র আদর্শের কথা ভুলেও উচ্চারণ করে না। দাবীদাওয়া, বিক্ষোভ, কর্মবিরতি প্রায়শঃ দৃষ্ট। নিমাইসাধনের মতে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক রচনায় ‘আংশিক সফল’, চাকুরি মনস্কতায়ও তাই। ৪) বিশ্বভারতী বীরভূম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত এ ক্ষোভ সঙ্গত। আর এক উপাচার্য অম্লান দত্ত-ও একটি দৈনিকে বিশ্বভারতীকে গ্রাম্য কলেজের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ৫) শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন পাঠভবন ও শিক্ষাসত্র সমমর্যাদা পায় না যা অভিপ্রেত ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। দেখেছি হলকর্ষণ, মাঘমেলা ইত্যাদিতে শান্তিনিকেতনের ছাত্র/শিক্ষকের কোনো আগ্রহ নেই। ৬) বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত হওয়ায়, ইউ.জি.সি.র যান্ত্রিক ফতোয়া চালিত হওয়ায় স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে একথা বহুজনে বলেছেন, বহু আগে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বা সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ও বলেছিলেন। নিমাইসাধনবাবুর কথা ঠিকই — ‘রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্রের মূল আদর্শ প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।’ এটি শান্তিনিকেতন অঞ্চলের আর একটি স্কুল মাত্র, যার গরিমা নেই।
মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাদর্শের কথা বারবার বলেছেন, যা বহুমুখী শিক্ষার সামগ্রিকতা পেতে চায়, যাতে ত্যাগ, সেবা, কায়িক ও মানসিক শ্রমের, প্রাচীন জীবনাদর্শ ও নবীন জ্ঞানালোকের সম্মীলন প্রত্যাশিত তার সঙ্গে জীবিকা ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার দ্বন্দ্বে দ্বিতীয়টির ক্রমপ্রাধান্য এবং রবীন্দ্র আদর্শ পিছু হঠছে। কলাভবনের ঐতিহ্য ও মর্যাদা অস্বীকার করি না। কিন্তু এখান থেকে একজনও প্রথম শ্রেণীর শিল্পী গত ৪০/৫০ বছরে তৈরী হয় নি। নন্দলাল বসু, সুব্রহ্মনিয়ম, সোমনাথ হোড়, রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারীর কাল স্বর্ণযুগ এবং সে যুগেও পারস্পরিক বিরোধ ছিল, বিমূর্ত-শিল্প শিক্ষা ও শিক্ষণ চালু করতে বেগ পেতে হয়, রামকিঙ্কর তাঁর প্রথাবিরোধী শিল্প ও জীবনযাপনের জন্য বহুনিন্দিত হন। কলাভবন নিম্ন ও মধ্যমেধার শিল্প জন্ম দিচ্ছে, প্রদর্শনী দেখতে দেখতে সে কথাই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সাধক-শিক্ষক, চেয়েছিলেন আত্মোৎসর্গ-পরায়ণ, সেবাব্রতী জ্ঞান-সাধক, চেয়েছিলেন ছাত্রজনের সখা শিক্ষক। সে আদর্শ সতীশচন্দ্র, অজিত চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন, বিধুশেখর প্রভৃতির মতো কিছু শিক্ষকের মধ্যে দেখা যেত। রবীন্দ্রনাথ যতদিন সক্রিয় ছিলেন বিদেশ থেকে সত্যকার জ্ঞান উৎসুক শিক্ষক গবেষক এসেছেন। রবীন্দ্র প্রয়াণের পর বহুদিন চলে গেছে। রবীন্দ্র শিল্পাদর্শ স্তিমিত, তাই বিদেশী গবেষক বিরল। পারস্পরিক মনান্তর, মতান্তরে রবীন্দ্র জীবৎকালেই ক্ষিতিমোহন, বিধুশেখর, মোহিত সেন, দীনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকে আশ্রম ত্যাগ করেছেন। সমকালের কেউ কেউ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন কানপাতলা, স্তাবকতা পছন্দ করতেন। ফলে রবীন্দ্রসান্নিধ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। রথীন্দ্রনাথের কালেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে, রথীন্দ্র আশ্রম ত্যাগ করেন, উত্তরায়ণেই বৈঠক বসত রথীন্দ্রস্তাবক দলের। তাঁকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র একেবারে অজানা নয়। ১৯৩৮-এই রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে জটিল অবস্থার কথা লিখছেন। জীবনসায়াহ্নে বিশ্বভারতীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহাত্মা গান্ধীর কাছে আবেদন করেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন নি তাঁর শিক্ষাদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গান্ধীজী উপযুক্ত নন। কারণ, শিক্ষার সর্বতোমুখিতা, শিক্ষার গভীরতা কোনোটিই গান্ধী আদর্শে ছিল না। গান্ধীর রাজনীতি চিন্তা রবীন্দ্রচিন্তার অনুকূলে ছিল না। ‘রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের মানুষকে হাতের কাজ শিখিয়ে কুটির শিল্পকে উৎসাহদান করে, পারিবারিক বৃত্তি বা পেশাগত বিদ্যাকে উন্নত করার শিক্ষাদান করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নত ও স্বনির্ভর করা।’ (ভগ্ননীড় বিশ্বভারতী; পৃ. ৫১) এ উদ্দেশ্য কি সার্থক হয়েছিল? হ্যাঁ - অল্প কিছুদিনের জন্য। তারপর সে আশা জলাঞ্জলি হয়েছে। শান্তিনিকেতন বাজারে, কলকাতায় সে মালের দাম বেশী বলে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যেতে বাধ্য। কো-অপারেটিভ একটি আছে কেন্দ্রস্থলে, তার বিক্রি কম নয়। কিন্তু ভুবনডাঙার ব্যাপ্ত বাজারে কেনাকাটার পরিমাণ অনেক বেশী, কলকাতা থেকে আমদানী মালেরও যথেষ্ট চাহিদা।
নিমাইসাধনের পর্যবেক্ষণ যথার্থ — ‘বিশ্বাস ও বাস্তবের মধ্যে বিরোধ ও ব্যবধান ক্রমেই প্রকট’ যা রবীন্দ্রনাথকেও ‘ক্ষোভ ও হতাশায়’ বিচলিত করে। রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা ও শান্তিনিকেতন ঐতিহ্যের ‘রেশটুকু’ এখনও আছে। (পৃ. ৭১) ১৯৯১-এ বইটি লেখা। আমি চাকরি করতে গিয়ে ক্ষয়ের ক্রমবর্ধমানতা দেখেছি। প্রাত:কালীন উপাসনায় (তখন সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল) শিক্ষকদের দেখতে পেতাম না। বেশ কিছু বিভাগ স্থানান্তরিত হলে সেই সেই বিভাগে উপাসনা উঠে গেছে। কারণ — ‘রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা, জীবনচর্চায় প্রকৃত আস্থা, তার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব।’ (ঐ, পৃ. ৭৩) শান্তিনিকেতনের মেলা বা উৎসবের পরে পরে গৌর প্রাঙ্গণে মদের বোতলের ছড়াছড়িতে আমরা মাঠে ক্লাস নিতে পারতাম না। ৯১-তেই উপাচার্য লক্ষ্য করেছেন মতের অমিল, রাজনৈতিক ভাবনার অমিল কালো ছায়া ফেলেছে আশ্রমে। হোস্টেলে খাবার অতি নিম্ন মানের হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়ত।
বিশ্বভারতীর বর্তমান সমস্যা, তার প্রতিকার কিভাবে হবে এ-নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ১৯৫১ সাল থেকে। রবীন্দ্র ভাবিত সমাজ সংগঠনের আদর্শ, আত্মআস্থা নির্ভরশীলতা ভালো, যদি রাষ্ট্র এবং মহাজন-জমিদার-স্বার্থ নাক না গলায়। রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও কৃষি উন্নয়নে যেসব ভেবেছিলেন তার উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ কোনো ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নতির কথা ভাবেন নি, বরং বারংবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও পরিকল্পনা করে গেছেন। কিন্তু ঘটনা হল এই যে তিনি বিশ্বভারতী এবং শ্রীনিকেতন নিয়ে, তার নানা সমস্যা সংকটে ক্রমান্বয়ে হতাশ হয়েছেন। এজন্য তাঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ, পতিসরে, শ্রীনিকেতন ও বোলপুরে যে অবস্থায় কাজ শুরু করতে চেষ্টা করেন তখন এই দুই কেন্দ্রের সমাজ ছিল বেশ খানিকটা অনুকূল। ফলে সাফল্য এসেছে। দ্বিতীয়ত: উভয় স্থানে পেয়েছেন ডেডিকেটেড, কমিটেড বেশ কিছু কর্মী যাঁরা হাতে কলমে কাজে নেমেছেন। তৃতীয়ত: রাষ্ট্র বা রাজনৈতিকতার ক্রমবর্ধমান খবরদারি কম ছিল। এখন বিশ্বভারতীকে সব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের আমলা ও মন্ত্রীদের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। এই সর্বভারতীয় আমলা ও মন্ত্রীরা রবীন্দ্র সমাজ গঠন আদর্শ বোঝে না, বুঝতে চায় না। তাই বিশ্বভারতীর ‘স্বাতন্ত্র্য’ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাদের কাছে এটি ভারতের আর একটি অর্থপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র। বীরভূম রাজনীতির ঝাপটা যথেষ্ঠ আছে। চতুর্থত: সমাজ গত-কয়েক দশকে ব্যাপক ভাবে বদলে গেছে। ভোগ্যপণ্যনির্ভর সমাজ, অর্থসর্বস্বতা, চাকরি মনস্কতার অতিরেক, পুরোনো মূল্যবোধে অনাস্থা রবীন্দ্রআদর্শ রূপায়ণে অন্তরায়। তবু বিশ্বভারতীর গ্ল্যামার তারা বাইরে থেকে বজায় রাখতে চায়। গ্ল্যামারই বড় কথা। বিশ্বভারতীর ধারে কাছে ফ্ল্যাট কমপ্লেক্স, ছুটি ছাটায় একটু রবীন্দ্র কালচার, ব্যাপক সুটিং হাসির প্রেরণা জোগায়। তাই রবীন্দ্র আদর্শের দুর্গতি নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। খাল কেটে কুমীর ডাকা হয়েছে।
অনেকে অনেকভাবে প্রাণপণে আশা করে যাবেন। আশা করার অধিকার সবার আছে। যাবতীয় মহৎপ্রচেষ্টার মরণ হতেই পারে — এ ভাবনা তিরস্কৃত হোক কামনা করি।
শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ব্যক্তিগত দুঃখকষ্টের মধ্যে চাকরি করেছি বলে, শিক্ষক অশিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছি বলে আজও বার্ধক্যে, অসুস্থতা তুচ্ছ করেও যখন শান্তিনিকেতন যাই তখন দোকানি, রিকশাওলারা দু-দণ্ড ডেকে কথা বলে। মনে পড়ে দুপুরের রোদে ক্লান্ত শরীর নিয়ে যখন ঘরে ফিরতাম রান্না চাপাব বলে তখন রাস্তায় ঢোকরা শিল্পীরা ক্রেতার আশায় বসে থাকত। ছাত্রী মেয়েরা ওদের পাশে বসে রঙিন কারে গলার মালা বুনে নিত। কর্তৃপক্ষের আদেশে সে-সব গেছে। শান্তিনিকেতন পায়ে হেঁটে ঘুরতাম অবসরে। পাঁচিলে পাঁচিলে স্বেচ্ছাবিহারের সেসব পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাঁওতাল ও অন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের পাড়া পাঁচিলের বাইরে। তারাও আদিবাসীত্ব ঘোচাতে চাইছে। চটকদার গেট হচ্ছে, নানা চকমিলান বাড়ি হচ্ছে, উঁচু বাড়ি হচ্ছে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। হয়তো সেসব জরুরী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসব চাননি।
আমার কথায় নেতির ভাগ অত্যধিক। শান্তিনিকেতনে পড়াতে আসার আগে শালবীথিতে রবীন্দ্রনাথকে কল্পনায় উদ্ভাসিত দেখতাম। চাকরি করতে করতে সেই রবীন্দ্রনাথ হারিয়ে গেছেন আমার মন থেকে। তবু আজও যখন দেখি সুদূর গ্রামের মানুষ দলে দলে এসে রাস্তার পুকুরে স্নান ক’রে, এখানে ওখানে খেয়ে, চলেছে রবীন্দ্রবাড়িগুলি দেখতে তখন ভালো লাগে। আর কোনো কবির জন্য এমন কি হয়েছে? নিশ্চয়ই না। জীবনসায়াহ্নে এসে রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। জীবনের অভিজ্ঞতা, শ্রুত সমস্যা ও রবীন্দ্র রচনাবলীর দ্বন্দ্ব — মাঝে মধ্যে আজও ভাবায় বৈকি।
একুশে সংবাদ/এস কে
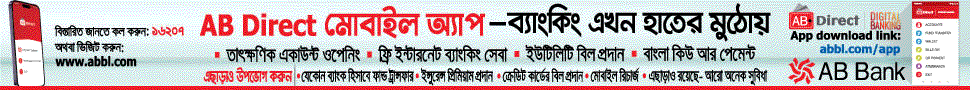






 একুশে সংবাদের সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি অনুসরণ করুন
একুশে সংবাদের সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি অনুসরণ করুন









আপনার মতামত লিখুন :